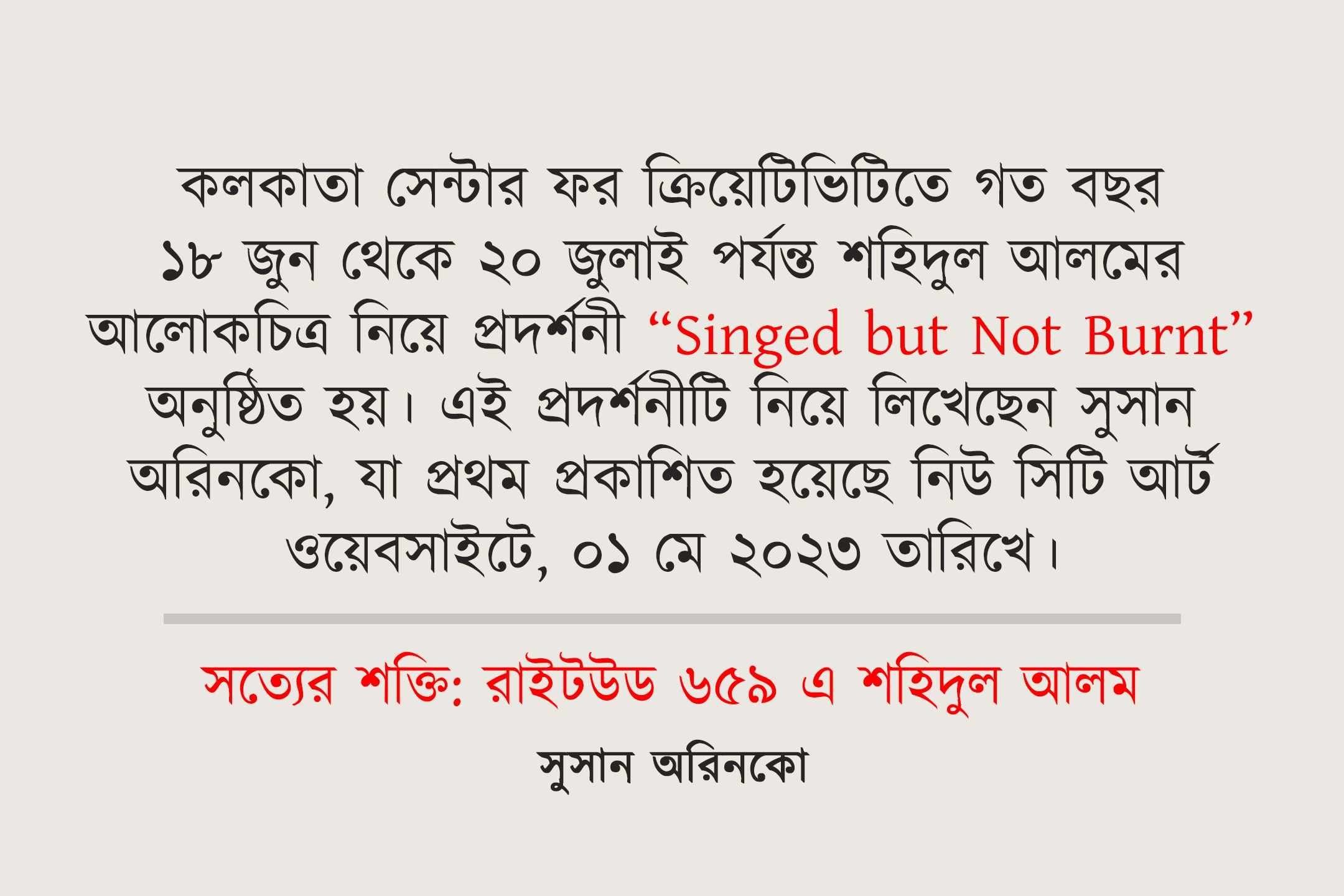বৈসু, সাংগ্রাই, বা বিঝু যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এটি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক জনগোষ্ঠীর মানুষদের একটি ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তম সামাজিক উৎসব। সুপ্রাচীন কাল থেকেই উৎসবটি আড়ম্বরের সাথে উদযাপিত হয়ে আসছে। উল্লিখিত জনগোষ্ঠীগুলো বহুকাল থেকেই এ উৎসব পালন করে আসলেও কবে, কোন্ শতাব্দী থেকে এর পত্তন ঘটেছিল, তার সঠিক কোনো লিখিত তথ্য পাওয়া যায় নি। ইতিহাসের পাতায় আমরা প্রথম লিখিতভাবে বিঝুর আড়ম্বরপূর্ণ রূপ দেখতে পাই চাকমা রাণী কালিন্দীর আমল থেকে। রাণী কালিন্দী বাংলা ১২৭৩ সনে চট্টগ্রামের রাজানগরে মহামুণি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের পাশে একটি দীঘি খনন করেন। পরবর্তীকালে এই দীঘিকে ঘিরেই প্রতি বছর বিঝুর সময় মাসব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়। বিঝু উৎসবে আয়োজিত বৌদ্ধ মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার দূরদূরান্ত থেকে তিন-চারদিন পায়ে হেঁটে পাহাড়িরা মেলায় আসতেন। মহামুণি মেলাটি ছিল একইসাথে ধর্মীয় ও সামাজিক। একই ভাবনা থেকে বর্তমানে খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে মহামুণি মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।
তৎকালীন সময়ে রাজানগরের মহামুণি মেলার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকত পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ বাহিনী। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন লুইন মেলা পরিদর্শনে এসে মহামুণি মেলার অভিজ্ঞতার কথা তার রচিত Fly on the Wheel বইয়ে লেখেন – “...but here in the hill tracts throughout three days carnival, I had not seen one drunken man nor witnessed any discourtesy to any women. They are honest, kindly people, happy in their homes and in their Buddhist faith. I doubted much if they had anything to gain from the introduction of European ideas.” [সূত্র: শরদিন্দু শেখর চাকমা (২০০২) পার্বত্য চট্টগ্রামের একাল সেকাল, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা]
মূলত চৈত্র মাস ঘনিয়ে এলেই পাহাড় বাংলা বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ করা ভালো, বিঝু উৎসবের সাথে জুমচাষেরও একটা নিবিড় সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। চৈত্র মাসের শুরুর দিকে জুম পাহাড়ের আগাছা পরিষ্কার করে সেগুলো পুড়িয়ে জুমচাষের উপযোগী করে তোলা হয়। পরবর্তীতে কয়েক পশলা বৃষ্টির পরে জুমে ধানসহ বিভিন্ন ধরনের বীজ বোনা হয়। এসময় জুম পাহাড়ের রুক্ষতা কচি সবুজের আবরণে ঢাকা পড়ে। তখন পাহাড়িদের মনে বিঝুর আনন্দ আর এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে জুমচাষের ধুম পড়ে যায়।

সপরিবারে ঐতিহ্যবাহী জুম চাষে ব্যস্ত একটি আদিবাসী পরিবার
আলোকচিত্র 
 ঙানচং ম্রো
ঙানচং ম্রো
বৈসু, সাংগ্রাই, বিঝু (বৈসাবি) হল এমন একটি সামাজিক উৎসব যেটি অতীতের সব ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রেরণা জোগায়। বাংলাদেশে বোধহয় বৈসাবি উৎসবই একমাত্র উৎসব যেখানে ধর্মীয় আবহ নেই, কিন্তু যা সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতির মাধ্যমে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ রচনা করে।
বৈসাবি তিন পর্বে তিন দিনে সম্পন্ন হয়। চৈত্র মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখ এবং বৈশাখ মাসের ১ তারিখ – এ তিনদিন যথাক্রমে প্রস্তুতি পর্ব, মূল উৎসব ও বর্ষবরণ বা চাকমাদের গোজ্জেপোজ্জে দিন। প্রস্তুতি পর্বকে চাকমারা ‘ফুল বিঝু’, মারমারা ‘পাইংছোয়ে নিহ্’, ত্রিপুরারা ‘হারিবৈসু’ বলে। ফুল বিঝু বা হারিবৈসু’র দিন ভোররাত থেকে ছেলেমেয়েরা ঝাড়-জঙ্গল বা বাগান থেকে নানান জাতের ফুল সংগ্রহ করে। সংগৃহীত ফুলগুলোর কিছু অংশ কলাপাতায় তুলে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এর পেছনে এই বিশ্বাসটুকু কাজ করে যে, ফুলগুলোর সাথে বিগত বছরের সব দুঃখ ও গ্লানি ধুয়েমুছে যাবে। নদীর স্রোতে ফুল ভাসানোর পরে শিশুরা নদীর পানিতে ডুব দিয়ে গোসল করে ‘বিঝুগুলো’ (কল্পনার রসগোল্লা!) খাওয়ার লোভে! বয়স্করা এ দিন মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সকলের মঙ্গল কামনা করেন। সন্ধ্যায় ঘরের মূল দরজা ও প্রতিটি ঘরের কোণে এবং নদীতে গিয়ে গঙ্গা মায়ের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে পরিবারের সুখসমৃদ্ধি কামনা করা হয়। এছাড়া এ দিন গবাদি পশুকে গোসল করিয়ে ফুলের মালা পরানো হয় এবং পরবর্তী তিন দিনের জন্য পশুদের বিশ্রাম দেয়া হয়।
চৈত্র মাসের ৩০ তারিখে হল মূল উৎসব। এ দিনটিকে চাকমা ভাষায় ’মূল বিঝু’, ত্রিপুরা ভাষায় ‘বিসুমা’ আর মারমা ভাষায় ‘আল্লেনিহ্ সাংগ্রাই’ বলে। এ দিন ছেলেমেয়েরা ভোরে ঘুম থেকে উঠে গ্রামের প্রতিটি বাড়ির উঠানে গিয়ে ওই বাড়ির হাঁস, মুরগি, কবুতরের জন্য ধান, চাল, গম ছিটিয়ে দিয়ে আসে। এর অর্থ হল, জগতের সব প্রাণী ভরা পেটে থাকুক ও সুখী হোক। এরপর নদী থেকে জল তুলে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বয়স্কদের গোসল করানো হয়। এ গোসলের মাধ্যমে কনিষ্ঠজনেরা বয়স্কদের আর্শীবাদ গ্রহণ করে। সকালের এসব পর্ব শেষ হওয়ার পর থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানোর পালা শুরু হয়ে যায়। মূল বিঝু বা বিসুমা’র মূল ব্যঞ্জন হলো ‘পাজন’, যা নানান রকম সবজির সংমিশ্রণে রান্না করে অতিথিদের পরিবেশন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পুকুর ঘাটে ফুল বিজুর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে উৎসবে অংশ নিচ্ছেন পাহাড়ের জুম্ম শিক্ষার্থীরা।। (১২ এপ্রিল, ২০২২)
আলোকচিত্র 
 সুপন্ত চাকমা
সুপন্ত চাকমা
নতুন বছরের প্রথম দিনটি চাকমাদের কাছে ‘গোজ্জেপোজ্জে’ দিন। অর্থাৎ গড়াগড়ি বা বিশ্রাম নেওয়ার দিন! এ দিনটিকে মারমারা বলে ‘আছুংনিহ্ সাংগ্রাই’, ত্রিপুরারা বলে ‘বিসিকাতাল।’ নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এ দিন ঘরে ভালো খাবারদাবারের আয়োজন করা হয়। নতুন বছরে সবার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে তিন দিনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। যদিও আজকাল সপ্তাহব্যাপী বিঝুর আমেজ রয়ে যায়!
সময়ের পরিক্রমায় পাহাড়ি সমাজ থেকে অনেক পুরোনো ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা হারিয়ে যাচ্ছে। সারাবছর সেসব খেলাধুলা চর্চার সুযোগ না থাকলেও বিঝুর সময় গ্রামে গ্রামে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এতে প্রবীণরা যেমন শৈশবের সুখস্মৃতি ফিরে পান, তেমনি নতুন প্রজন্মকে সেসব খেলাধুলা নতুন প্রেরণা জোগায়। ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার মধ্যে চাকমাদের ঘিলা খেলা, নাদেং খেলা, মারমাদের অতি জনপ্রিয় পানিখেলা, ত্রিপুরাদের গরিয়া নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গরিয়া হলো কর্ম ও প্রেমের দেবতা। নৃত্যের মাধ্যমে নতুন বছরে এ দেবতাকে স্মরণ করে ত্রিপুরারা কর্মের শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চয় করেন।
বাঙালি সমাজের চৈত্র সংক্রান্তি আর পাহাড়ের বৈসাবি উৎসব উভয়ই অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক। বৈসাবি যেমন পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ তৈরি করে, তেমনি বাঙালির চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখে পান্তা ভাত আয়োজনের মধ্যে রয়েছে আবহমান প্রাচীন বাংলার একটা সুগভীর বন্ধন, যে বন্ধনে ছিল না কোনো জাতপাত কিংবা ধর্মের ভেদাভেদ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, সমাজ আর বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই আগেকার বন্ধনগুলো ছিন্ন হতে হতে বর্তমানে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এখন আস্থার সংকট তৈরি হয়ে বেড়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আর অন্য সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে অসম্মান করার প্রবণতা।
২.
পাহাড়ে বৈসাবি উৎসবের যতটা আনন্দ বয়ে আনার কথা, ততটা আনন্দের ফল্গুধারা পাহাড়ে কি আদৌ বহে? বিগত বছরগুলোর দিকে তাকালে আমরা সেই ভয়ের সংস্কৃতিটাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারব। বৈসাবি উৎসবের আমেজ শুরু হওয়ার আগে বা আমেজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই বারবার পাহাড়িদের ওপর কোনো না কোনো সাম্প্রদায়িক আঘাত এসেছে। ত্রিশ বছর পরেও কি আমরা ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিলের লোগাং গণহত্যার কথা ভুলতে পেরেছি? আমরা ভুলে যেতে পারি না ১৯৮৪ সালের ৩১ মের রাঙামাটির ভূষণছড়া-হরিণা কিংবা ১৯৮৬ সালের ১ মের পানছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়িতে পাহাড়িদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা! ১ মে’র খাগড়াছড়ির মাজন পাড়া জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনাটার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে দৃশ্যটা আজও আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে! কীভাবে ভুলে যাব ১৯৮৯ সালের ৪ মে’র লংগদুর গণহত্যার কথা! যে গণহত্যার প্রতিবাদ জানাতে এরশাদের সামরিক শাসনের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে ৮৯’এর ৪ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গঠিত হয়েছিল! ২০১০ সালে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটি জেলার বাঘাইহাট ও খাগড়াছড়ি জেলা শহরে দুদিন ব্যাপী যে তাণ্ডব আর সহিংস সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছিল, যে হামলায় বাঘাইহাটে লক্ষীবিজয় চাকমা ও বুদ্ধপুদি চাকমা নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, কীভাবে তাঁদের তক্তার মতন পড়ে থাকা লাশের কথা ভুলে যাই! ক্রন্দনরত বুদ্ধপুদি চাকমার সন্তানদের মুখগুলো যখন পরদিন জাতীয় পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল, এরপরও কি আনন্দ নিয়ে নির্বিঘ্নে বিঝু উদযাপন করা যায়? এভাবে আর কতো হিসাবের খাতা উল্টাব! তাই বৈসাবি যতটা না আনন্দের, তার চাইতে মনের অদৃশ্য ভয় আমাদেরকে অনেক বেশি কুঁকড়ে রাখে!
বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(১)-এ বলা হয়েছে, “সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।” কিন্তু এদেশের আদিবাসীরা যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমান সুযোগ পাচ্ছে না তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। সেসব প্রসঙ্গে না গিয়ে আমি আজকের বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। ঈদ, পূজা পার্বণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বভাবতই বন্ধ থাকে। কিন্তু প্রতিনিয়ত সহিংস ঘটনার শিকার হয়ে আদিবাসী শিশুরা যে ভয়ের সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠছে, বিঝুর সময় পরীক্ষার চাপ তাতে যুক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে আদিবাসী শিশুদের মনোজগতে বিরাট এক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশার বিষয় হল, বর্তমানে সরকারি পঞ্জিকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য ১৩ এপ্রিল (৩০ চৈত্র) ঐচ্ছিক ছুটি রাখা হয়েছে, যেটা আগে ছিল না। তাই এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু যে বিষয়টির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেটি হল: NAPE (National Academy for Primary Education), শিক্ষা অধিদপ্তর বা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যেখান থেকেই বিদ্যায়তনিক পঞ্জিকা প্রণয়ন করা হোক না কেন, এটি প্রণয়নের সময় যেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসবটাকে বিবেচনায় রেখে পরীক্ষার সময়সূচী ও ছুটির তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বিশেষ করে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার মতন পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে।
এখানে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সব কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার আংশিক মাত্র পরিচালিত হচ্ছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখনো জাতীয়ভাবে গৃহীত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় সামাজিক এই উৎসবটি যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ে পালিত হয় (এটি চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে না) তাই বিদ্যায়তনিক ছুটির তালিকা বা পরীক্ষার সময়সূচিতে সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব।
বৈসাবি উৎসব উপলক্ষ্যে জাতীয়ভাবে সরকারি ছুটি না থাকায় শিক্ষার্থীদের মতন চাকরিজীবীদেরও বিভিন্ন সময়ে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারিভাবে ঐচ্ছিক বা সংরক্ষিত ছুটির বিধান থাকলেও এ ছুটির অনুমোদন নিতে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর অনেক সময় নির্ভর করা লাগে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এমনও দৃষ্টান্ত আছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা জরুরি কাজের অজুহাতে বিঝুর দিন আদিবাসী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দিয়ে অফিস করিয়ে থাকেন। এতে ওই পাহাড়ি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেই ব্যাখ্যা কে দেবে!
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম। সেখানে বাঙালি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ছাড়াও আরও তেরটি জাতিসত্তা রয়েছে এবং সেসব জাতিসত্তার রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। তাই ওই অঞ্চলের অন্যতম সামাজিক উৎসবকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারিভাবে ন্যূনতম দুদিন ছুটি নির্ধারণ করা উচিত। এতে পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসমূহের স্বাতন্ত্রবোধের প্রতি যেমন সম্মান জানানো হবে ।
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম। সেখানে বাঙালি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ছাড়াও আরও তেরটি জাতিসত্তা রয়েছে এবং সেসব জাতিসত্তার রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। তাই ওই অঞ্চলের অন্যতম সামাজিক উৎসবকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারিভাবে ন্যূনতম দুদিন ছুটি নির্ধারণ করা উচিত। এতে পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসমূহের স্বাতন্ত্রবোধের প্রতি যেমন সম্মান জানানো হবে, তেমনি দেশের সমতলের জনগোষ্ঠীও পাহাড়ের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এবং এ সামাজিক উৎসব সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। এ বিষয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নজর দেয়া জরুরি।
পরিশেষে আমরা চাই সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এমন একটি বাংলাদেশ, যেখানে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক চেতনার উর্ধ্বে উঠে সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি, ঐক্য ও পারস্পরিক সম্মানবোধ তৈরি হবে। বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির দেশ। তাই সব জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠলেই তবে বাংলাদেশ জাতিতে, সংস্কৃতিতে, চিন্তা ও মননে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হবে। সংখ্যাগত বিচারে পেশিশক্তি ও ক্ষমতার দম্ভে নয়, দেশের সব জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরির মধ্য দিয়েই বাংলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে।